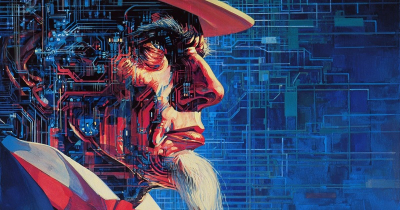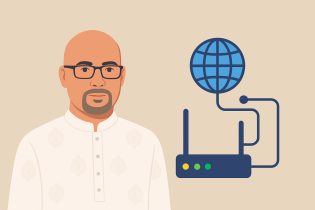‘ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫’ ডেটার নিয়ন্ত্রণ কার হাতে
রাষ্ট্রের নজরদারি না নাগরিকের নিয়ন্ত্রণ?
শাহিদ বাপ্পি
প্রকাশ: ০৫:০৯, ১৫ অক্টোবর ২০২৫ | আপডেট: ১০:৫০, ২৭ অক্টোবর ২০২৫

ছবি, যমুনা টিভির সৌজন্যে
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নামে শুরু হয় নজরদারি, আর সেখানেই জন্ম নেয় স্বাধীনতার প্রশ্ন। কোথায় শেষ হবে সেই নজরদারির সীমা, আর কোথা থেকে শুরু হবে নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকার এই দ্বন্দ্বই এখন ডিজিটাল বাংলাদেশের নতুন বাস্তবতা। সম্প্রতি অনুমোদিত ‘ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫’ সেই সীমারেখাকেই নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে একদিকে এটি রাষ্ট্রের ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, অন্যদিকে নাগরিক স্বাধীনতার নতুন বিতর্কের সূচনা।
একটি আইনের লক্ষ্য, আর তার নীতিগত প্রতিফলন: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে প্রণীত এই অধ্যাদেশটির উদ্দেশ্য স্পষ্ট। ডেটা ব্যবস্থাপনায় গোপনীয়তা, সুরক্ষা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা।
কিন্তু এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে গভীর নীতিগত প্রশ্ন: রাষ্ট্র যখন নাগরিকের তথ্যকে শ্রেণিবদ্ধ করে ‘উন্মুক্ত’, ‘অভ্যন্তরীণ’, ‘গোপনীয়’ ও ‘সীমাবদ্ধ’, তখন কি সে নাগরিকের স্বাধীনতার সীমানাও নির্ধারণ করে দিচ্ছে? ডেটার এই শ্রেণিবিন্যাস কেবল প্রশাসনিক নয়, বরং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাববাহী। কারণ তথ্যের মালিকানা মানেই এখন ক্ষমতার মালিকানা।
বাংলাদেশ এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সামনে দাঁড়িয়ে আছে-“ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫” এবং “জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫” কেবল আইনগত পরিবর্তন নয়, এটি ডিজিটাল যুগে রাষ্ট্র, নাগরিক এবং কর্পোরেট বিশ্বের মধ্যে নতুন ক্ষমতার সম্পর্ক গড়ে তুলছে।
এই দুই অধ্যাদেশের কেন্দ্রে রয়েছে মৌলিক প্রশ্ন: উপাত্তের মালিক কে? নাগরিক কি তাঁর নিজস্ব উপাত্তের মালিক, নাকি রাষ্ট্র সেই উপাত্তের অভিভাবক?
সম্মতির সীমা ও রাষ্ট্রের অব্যাহতি
অধ্যাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নাগরিকের ব্যক্তিগত উপাত্ত তার নিজের মালিকানাধীন এবং ব্যবহারের জন্য তার সম্মতি বাধ্যতামূলক। তবে ধারা ৩৭ অনুসারে, জাতীয় নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, জনশৃঙ্খলা, কর ফাঁকি প্রতিরোধ বা অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে। সরকার উপাত্তধারীর সম্মতি ছাড়াই তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করতে পারবে। এই ‘অব্যাহতি’ই এখন সবচেয়ে বিতর্কিত অংশ।
নীতিগতভাবে এটি রাষ্ট্রকে এমন এক ক্ষমতা দেয় যেখানে “জনস্বার্থ” নামের ব্যাখ্যাতীত একটি শব্দের আড়ালে। যে কোনো নাগরিকের গোপনীয়তাকে বৈধভাবে অতিক্রম করা সম্ভব। এটি কেবল প্রযুক্তিগত নয়, বর প্রশ্ন? রাষ্ট্র কি নাগরিকের অভিভাবক, না নাগরিকই রাষ্ট্রের উৎস?
ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব না নিয়ন্ত্রিত নাগরিকতা
বাংলাদেশ এখন ডিজিটাল অর্থনীতির কেন্দ্রে প্রবেশ করছে। ডেটা এখন নতুন পণ্য, নতুন মুদ্রা, নতুন ক্ষমতা। এই প্রেক্ষাপটে আইনটি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়াস হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কারণ আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রবাহ এখন বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার অংশ।
চীনের ডেটা লোকালাইজেশন নীতি, ইউরোপের জিডিপিআর, ভারতের ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট।
সব দেশই তাদের নাগরিকের ডেটাকে নিজস্ব সীমার মধ্যে সুরক্ষিত রাখতে চায়। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন: ডেটা যদি সার্বভৌম সম্পদ হয়, তবে তার আসল মালিক কে রাষ্ট্র না নাগরিক? যেখানে রাষ্ট্র নাগরিকের নামে সুরক্ষা দাবি করে, সেখানেই নাগরিকের আত্মনিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে প্রশাসনিক অনুমতিনির্ভর হয়ে যায়।
আন্তর্জাতিক রেফারেন্স ও তুলনামূলক পর্যালোচনা
বিশ্বব্যাপী গোপনীয়তার অধিকার এখন এক নতুন সাংবিধানিক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশন (জিডিপিআর) থেকে শুরু করে ভারতের ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট (ডিপিডিপি) । সব দেশই নাগরিকের উপাত্ত সুরক্ষাকে রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে দেখছে। কিন্তু বাংলাদেশের খসড়া আইনে সরকার নিজেই একটি ব্যতিক্রমধারা সংরক্ষণ করেছে, যা কার্যত উপাত্ত নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছে।
ইউরোপীয় জিডিপিআর অনুযায়ী ডেটা প্রক্রিয়াকরণ কেবল নাগরিকের স্পষ্ট সম্মতির ভিত্তিতে হতে পারে, এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থার প্রবেশাধিকার সীমিত হতে হবে বিচারবিভাগীয় অনুমোদনের মাধ্যমে। অন্যদিকে, সিঙ্গাপুরের পারসোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট (পিডিপিএ) কর্পোরেট দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার ওপর জোর দেয়।
কানাডায় “প্রাইভেসি কমিশনার” একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে, যেখানে নাগরিক সরাসরি অভিযোগ দায়ের করতে পারে।
অস্ট্রেলিয়ার অফিস অব দ্য অস্ট্রেলিয়ান ইনফরমেশন কমিশনার (ওএআইসি) নাগরিকের তথ্য অপব্যবহার বা নজরদারির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ করতে পারে।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত “ইন্ডিপেন্ডেট ডেটা অডিটর” ধারণার ভূমিকা, ক্ষমতা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে এখনো অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। এটি কার্যকর করতে হলে তাকে সাংবিধানিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে; তা না হলে এটি কেবল আনুষ্ঠানিক সংস্থা হিসেবেই থাকবে।
টিআইবির সমালোচনা ও নাগরিক উদ্বেগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সম্প্রতি জানিয়েছে, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও অংশীজন সম্পৃক্ততা ছাড়াই খসড়া অনুমোদন হতাশাজনক।
টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, “খসড়ায় আইনসম্মততা, ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মূলনীতি বাদ পড়েছে।
তিনি বলেন, "রাষ্ট্রীয় সংস্থার অনিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকার গোপনীয়তার মূল চেতনার পরিপন্থী।”
ধারা ২৪ এ ‘অপরাধ প্রতিরোধের’ নামে যে ঢালাও অব্যাহতির সুযোগ রাখা হয়েছে, তা ভবিষ্যতে নজরদারি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করতে পারে।
এই আইন যদি নাগরিকের সম্মতি ছাড়া উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের অনুমতি দেয়, তবে তা সাংবিধানিক অধিকারেরও লঙ্ঘন হতে পারে।
ডেটার অপব্যবহারকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে দেখানো ব্যবসা ও উদ্ভাবনের পরিসর সংকুচিত করতে পারে।
কারণ প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো তাদের নিজস্ব অ্যালগরিদম ও ইউজার ডেটার বিশ্লেষণ নিয়ে আইনি অনিশ্চয়তায় পড়বে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, রাষ্ট্রের লক্ষ্য যদি নাগরিকের উপাত্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়, তবে সেই নিরাপত্তার প্রথম শর্ত হলো নাগরিকের সম্মতি ও নিয়ন্ত্রণের নিশ্চয়তা।
প্রযুক্তি, নীতি ও নৈতিকতার সংযোগ
প্রাইভেসি এখন কেবল ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ধারণা নয় এটি এক সাংবিধানিক অধিকার।
এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দু রাষ্ট্র যদি নাগরিকের উপাত্ত নিয়ন্ত্রণের নামে সর্বত্র প্রবেশাধিকার রাখে, তবে তা এক প্রকার ডিজিটাল হেজিমনি তৈরি করবে যেখানে প্রযুক্তি হবে শাসনের হাতিয়ার, সুরক্ষার নয়।
আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া কনজু্মার প্রাইভেসি অ্যাক্ট (সিসিপিএ) নাগরিককে তার ব্যক্তিগত তথ্য মুছে ফেলার অধিকার দেয়। ইউরোপে ‘রাইট টু ফরগোটেন’ এখন স্বীকৃত মানবাধিকার।
বাংলাদেশেও যদি সেই অধিকার নিশ্চিত না হয়, তাহলে নাগরিক তার নিজ উপাত্তের উপর মালিকানা হারাবে।
আইনটি বাস্তবায়নে ভারসাম্য না রাখলে প্রযুক্তি, ফিনটেক, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা খাতে উদ্ভাবনের গতি কমে যাবে।
বিশেষ করে এআই ও মেশিন লার্নিং প্রকল্পে ডেটাসেট অনুমোদনের অনিশ্চয়তা গবেষণার অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করবে।
প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডেটা সুরক্ষা আইন মানে নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা।
এই নীতিই হওয়া উচিত বাংলাদেশের ডিজিটাল সার্বভৌমত্বের মেরুদণ্ড।
ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ ও প্রতিচিন্তা
বাংলাদেশ এখন ডিজিটাল অর্থনীতির কেন্দ্রভূমিতে প্রবেশ করছে। আগামী দশকে আন্তঃসীমান্ত বিনিয়োগ, ক্লাউড হোস্টিং, এআই সার্ভিস ও হেলথ ডেটা অ্যানালিটিকস হবে অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি।
একটি শক্তিশালী, নাগরিককেন্দ্রিক উপাত্ত সুরক্ষা আইন বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াবে, আউটসোর্সিং ও সফটওয়্যার খাতে প্রবৃদ্ধি আনবে।
কিন্তু আইনের ভাষা যদি দ্ব্যর্থক হয়, তাহলে তা নাগরিক স্বাধীনতা সীমিত করবে, কর্পোরেট কমপ্লায়েন্সের খরচ বাড়াবে এবং আন্তর্জাতিক আস্থা ক্ষুণ্ণ করবে।
রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক এখন প্রযুক্তিনির্ভর। যেখানে উপাত্তই নতুন মুদ্রা, সেখানে নাগরিকই হয়ে উঠছে সম্পদ, আর উপাত্ত হয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি।
এটাই ডিজিটাল সার্বভৌমত্বের নতুন বাস্তবতা। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আইন যদি সত্যিই অগ্রসর হতে চায়, তবে তাকে তিনটি নীতিকে সামনে আনতে হবে।
স্বচ্ছতা, সম্মতি এবং জবাবদিহি
রাষ্ট্র যদি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়, তবে নাগরিককেও নিশ্চিত করতে হবে যে তিনি নিজের উপাত্তের প্রকৃত মালিক।
যেখানে নাগরিক হয় উপাত্ত, আর উপাত্ত হয় রাষ্ট্রের সম্পদ।
সেখানেই শুরু হয় স্বাধীনতার নতুন পরীক্ষা।
একটি আইনের সীমা, একটি ভাবনার শুরু
‘ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫’ হয়তো বাংলাদেশের তথ্য সুরক্ষায় একটি কাঠামো দেবে।
কিন্তু তার প্রকৃত শক্তি নির্ভর করবে কতটা স্বাধীনভাবে এটি নাগরিকের অধিকারের জায়গায় দাঁড়াতে পারে তার ওপর।
প্রযুক্তি এখন কেবল উন্নয়নের উপাদান নয় এটি রাজনীতি, অর্থনীতি ও মানবিক মর্যাদার নতুন পরিসর।
রাষ্ট্র যদি সত্যিই নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়, তবে তাকে আগে নিশ্চিত করতে হবে নাগরিক যেন নিজেই নিজের উপাত্তের মালিক থাকে।
কারণ যেখানে নাগরিক হয় ডেটা, আর ডেটা হয় রাষ্ট্রের সম্পদ, সেখানেই শুরু হয় স্বাধীনতার নতুন পরীক্ষা।
শাহিদ বাপ্পি,হেড অব কনটেন্ট, টেকস্ক্রল। মতামত লেখকের নিজস্ব।